ICT News
খবরের শিরোনামঃ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে সেলফোন নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মালিকানা প্রশ্ন
খবরের তারিখঃ ২০১৫-১১-১০
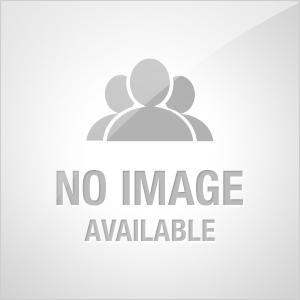 -খন্দকার সাখাওয়াত আলী
-খন্দকার সাখাওয়াত আলী
মোবাইল ফিন্যান্সসিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অপরিহার্য বাহন। দৃষ্টি কেড়েছে দেশী ও বিশ্বনেতৃত্বের। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সাফল্যের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে সরকারের নীতি-সিদ্ধান্ত ও সাহসী ভূমিকায়। বাংলাদেশে এমএফএস তার দ্বিতীয় প্রজন্মের যাত্রা করেছে। বাংলাদেশকে ঘিরে তাই মোবাইল কোম্পানি, বিশ্বব্যাংক, নেদারল্যান্ডসের রানী, বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, দেশীয় করপোরেট এনজিও, দেশী ব্যাংক ও দেশীয় করপোরেট মিডিয়া প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সব আগ্রহে কমতি কেবল ‘জাতীয় স্বার্থ’ ও ‘গ্রাহক স্বার্থ’র প্রশ্নে। এ আগ্রহের প্রধান ভিত্তিটি আমাদের ভবিষ্যতের ‘বাজার-আয়তন’ ও তৃণমূল পর্যায়ের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইউএসএসডি টেকনিক্যাল কমিটিতে নাগরিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। একজন সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ গবেষক হিসেবে কমিটিতে বসে একদিকে আমার যেমন সকল অংশীজনের মনোভাব ও চাহিদা বোঝার সুযোগ হয়েছিল, অন্যদিকে এ খাতের বাজার পরিধি ও পরিসরের গভীরতা এবং ভবিষ্যত্ চ্যালেঞ্জগুলো ধাপে ধাপে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। ‘জাতীয় স্বার্থ’ ও ‘গ্রাহক স্বার্থ’র দিকটি বিবেচনায় রেখেই এ লেখায় আমার নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছি।
বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে এমএফএসের জন্য গাইডলাইন তৈরি করে, যেখানে তারা এমএফএসের ওপর মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের (এমএনও) নেতৃত্ব কিংবা কর্তৃত্ব করার বিষয়টিকে খারিজ করে দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক থেকে সিদ্ধান্তটি অবশ্যই সুচিন্তিত-ভাবনাপ্রসূত ও দৃঢ় অবস্থানের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছিল। ফলে এ গাইডলাইনের ভিত্তিতে মাত্র চার বছরে এ খাত বড় ধরনের সাফল্য দেখাতে পেরেছে। সুনির্দিষ্ট এ গাইডলাইনের ভিত্তিতে এমএফএস সেক্টরের দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। ফল হিসেবে তাই আমরা দেখি, গ্রাহক সংখ্যা শূন্য থেকে তিন কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে এমএফএসে ৩৫ লাখের বেশি আর্থিক লেনদেন হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় এমএফএস খাতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ এরই মধ্যে একটি সফল এমএফএস ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক এমএনও-লেড মডেল গ্রহণ না করার পর থেকে এমএনওগুলো এ ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার জন্য নিজেদের পক্ষে নানা ধরনের প্রচারণা ও কৌশল অব্যাহত রেখেছিল, যা চলমান। গাইডলাইন তৈরির পর প্রথম দু-তিন বছর এমএনওগুলো দাবি করল, তারাই কেবল এককভাবে ব্যাংকের চেয়ে দ্রুততার সঙ্গে এমএফএসের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাবহির্ভূত কোটি কোটি মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছাতে পারবে। অন্যদিকে এমএফএস প্রদানকারীরা এ খাতের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে এ সেবা দেয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে। তাই দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ আজ এ সেবা সফলভাবে পাচ্ছে। ফলে এমএনওর দেয়া প্রাথমিক সে যুক্তি ধোপে টেকেনি।
আগেই বলেছি, এমএনওগুলো এ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশের জন্য গোড়া থেকে বেশ চাপ দিয়ে চলেছে। নিজেদের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখাতে এমএফএস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে অবাস্তব ও অসত্য সব তথ্য বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এমএফএসের সফলতম প্রতিষ্ঠান বিকাশকে ক্ষেত্রবিশেষে অপবাদ দেয়া হচ্ছে মনোপলি বলে। বাস্তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৭টি লাইসেন্স ইস্যু করেছে এবং তাদের মধ্যে ১০টি কাজ শুরু করেছে, যা বর্তমানে সক্রিয়; বিকাশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এমএফএসের সংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক। কিছুদিন আগে আরেকটি এমএফএস কোম্পানি শিওর-ক্যাশ ৭০ লাখ ডলার নতুন করে বিনিয়োগ করেছে। বিকাশ, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকসহ সক্রিয় এমএফএসগুলো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে সেবা প্রদান করছে বাংলাদেশে। এছাড়া এ ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, তৃণমূল পর্যায়ে এজেন্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বজনীনভাবে ব্যবহার করছে। কাজেই বাস্তব জগত্ থেকে মনোপলি অবস্থান তাই অনেক দূরে। ২৭টি লাইসেন্সধারীর মধ্যে যাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল এবং প্রস্তুতি পর্বের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে শেষ করেছে, তারাই কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেছে। যারা ভালো করছে, অন্যরা তাদের কাছ থেকে শিখছে এবং বাজারে তাদের শেয়ার ধারাবাহিকভাবে বাড়াচ্ছে।
সম্প্রতি এমএফএসের সফলতার এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সঠিক নীতির ফলাফল হলো, যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের জন্য টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া, অর্থাত্ তাদের জন্য একটি সমতল খেলার মাঠ নিশ্চিত করা এবং অন্যায্য প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। সমতল খেলার মাঠ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে মূলধন আকর্ষিত হয় এবং তার ধারাবাহিকতায় দেশের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। লক্ষণীয়, একসময় এমএনও ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রামীণফোন ৮০ শতাংশ বাজার দখল করেছিল, কিন্তু অন্যরা ক্রমান্বয়ে শিখছে কীভাবে কাজ করতে হয়। তাই গ্রামীণফোনের মার্কেট শেয়ার বর্তমানে ৪২ শতাংশে নেমে এসেছে। নতুন কৌশল শেখা ও গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরিতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সময় দিতে হয়।
যখন কোনো একটি পক্ষ মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর হয়ে বলছে, এমএফএস ইন্ডাস্ট্রিতে এমএনওগুলো আরো বড় ধরনের প্রতিযোগিতা আনবে, তখন তাদের (মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর) এ খাতে প্রবেশের ফলে বিরাজমান প্রতিযোগিতায় কী ধরনের প্রভাব ও বাধার জন্ম দিতে পারে, তা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। তাই আমাদের ২০১১ সালের গাইডলাইন পুনর্নিরীক্ষণ করা উচিত যে, কী কারণে এমএনওর সম্পৃক্ততা এমএফএসের প্রসারকে কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং করে তুলবে। এ চ্যালেঞ্জের প্রধান পাঁচটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:
জবাবদিহিতা তৈরির চ্যালেঞ্জগুলো:
ক. নিয়ন্ত্রণ: আর্থিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালের গাইডলাইনে এমএনও-লেড মডেলটি খারিজ করে সঠিক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ দেশের নাগরিকদের অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের সুযোগ এমএনও-লেড মডেলে ছিল না। বিটিআরসি মুখ্যত এমএনও ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার দায়িত্ব পালন এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্যই মূলত এমএনও-লেড মডেলটি খারিজ করেছিল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিটিআরসির মধ্যে তাই কোনো দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।
খ. নিয়ন্ত্রণের বিকল্প পথ খোলা রাখা: সরকারের উচিত নিয়ন্ত্রণের বিকল্প পথ সবসময় উন্মুক্ত রাখা। এমএফএস নতুন এবং একই সময়ে কোটি কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এমএফএস ও এমএনওকে যদি আলাদা আলাদা করে রাখা হয়, তবে সরকার দুটি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে বোঝাপড়া করতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি দুটির কার্যক্রম, গঠন বৈশিষ্ট্য ও লাইসেন্সের শর্তগুলো এবং ম্যান্ডেটও আলাদা। অন্যদিকে এমএফএসকে উপলক্ষ করে এ দুই খাত যদি একবার একত্র হয়, তবে পরবর্তীতে তাদের আলাদা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে কেনিয়ার অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, একটি প্রভাবশালী এমএনও, এমএফএসে মনোপলি বা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করেছে।
গ. এমএনও ও এমএফএসের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক: এমএফএসের সব গ্রাহক কোনো না কোনো এমএনওর অংশীজন। স্বাভাবিকভাবেই তাই এমএফএস গ্রাহক এ এমএনও নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। এমএনওর আর্থিক সামর্থ্য অধিকাংশ এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ও মজবুত। কাজেই নেটওয়ার্ক নিয়ে নেটওয়ার্ক প্রভাইডার ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী এ সম্পর্কের টানাপড়েন খুব দ্রুত বড় আকারের বিরোধের জন্ম দিতে পারে। এ সম্পর্ক আরো জটিল হয়েছে, যখন এমএনওগুলো এমএফএসে মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। যতক্ষণ নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে পার্থক্য বা সুনির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যাতে করে উভয়পক্ষ ন্যায়বিচার পায়। উদ্ভূত বিরোধগুলো যেন তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে পারে। বিষয়টি অবশ্যই অবাস্তব হবে, যদি প্রতি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিটিআরসিকে বিরোধ মীমাংসার মধ্যস্থতা করতে হয়। এমএনও নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীলতার কথা বিবেচনায় রেখেই নিয়ন্ত্রকদের এমন গঠনপ্রণালি তৈরি করতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয় এবং উদ্ভূত বিরোধ বা দ্বন্দ্বের সমাধান হয়।
ঘ. এমএফএসের ঝুঁকি কমানো: বিশেষত আমরা যদি এমএফএসের সফলতার ব্যাপারে আন্তরিক হই, তবে অবশ্যই দেখতে হবে, এমএফএস স্বতন্ত্রভাবে কতটা কাজ করছে। কারণ এমএফএসের সফলতার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি ও গ্রাহকদের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর যথাযথ ও উপযুক্ত উদাহরণ হলো বিকাশ। বিকাশ সুনির্দিষ্টভাবে তার কাজের পরিধির মধ্যে থেকে মূলত ব্যাংকিং সেবাবহির্ভূত বিশাল জনগোষ্ঠীকে এমএফএস সেবা দিয়ে আসছে। গতানুগতিক এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিকাশের দৃশ্যমান পার্থক্য হলো, এমএফএসই বিকাশের মূল ফোকাস। সফলভাবে এ সুনির্দিষ্ট ও নিবেদিত কর্মপরিচালনার কারণেই বিকাশ তার অন্যান্য প্রতিযোগীর চেয়ে ভালো করছে। সেক্ষেত্রে নীতি তৈরিতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে— কী করলে দেশে আরো কিছু দেশীয় মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যায়।
সংজ্ঞাগত ও আর্থিক পরিধির বিবেচনায় এমএনওর জন্য বলতে গেলে এমএফএস খুবই ছোট আকারের ব্যবসা। কাজেই এমএনও যদি এমএফএসের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে, তবে বিষয়টি তাদের জন্য বড় কোনো ব্যাপার হবে না। কিন্তু এটা তখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন গরিব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর মূল গ্রাহক হয়ে ওঠে। এ অবস্থান মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সর্বোপরি এমএনওর ওপর এমএফএসের নির্ভরশীলতা এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যেহেতু একদিকে এমএনওগুলো এমএফএসের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল নয়, অন্যদিকে এমএফএসের অসফলতার ব্যাপারে এমএনওগুলোর কোনো নিয়ন্ত্রকের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই।
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ:
ক. নির্ভশীলতা কমানোর কৌশল: আগেই বলেছি, এমএফএসের সব গ্রাহক কোনো না কোনো এমএনওর অংশীজন এবং স্বাভাবিকভাবে এমএনওর নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। ফলে যদি এমএনওকে এমএফএস করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে এমএনওর মালিকানাধীন এমএফএসের গ্রাহকদের সঙ্গে অন্য এমএফএসের গ্রাহকদের অনিবার্যভাবেই একটি অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। এটা হবে বাজারের সাধারণ নিয়ম বা বিবেচনায় অনেকটা অনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং যা রীতিমতো গ্রাহকস্বার্থ ও অধিকারবিরোধী। কাজেই এমন একটি সময় আসতে পারে, যখন এমএনওগুলো পর্যায়ক্রমে তাদের প্রতিযোগীদের (অর্থাত্ ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি) পর্যাপ্ত অথবা কোনো নেটওয়ার্ক সুবিধা নাও দিতে পারে। তদুপরি যদি এমএনও এবং এমএফএসের মধ্যে সম্পর্কের সীমানা ও পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকে, তাহলে বিবদমান যেকোনো সমস্যা, বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সমাধান করতে নিয়ন্ত্রকদের (বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিটিআরসি) অনেক সময় ব্যয় করতে হতে পারে।
খ. প্রতিযোগিতাবিরোধী কৌশল: এমএনও, এমএফএসের ব্যবসার ভেতরে প্রবেশ করতে চায় শুধু মুনাফার জন্য এমনটা নয়। বরং তাদের মূল লক্ষ্য— এমএফএস ব্যবসাটির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া। আগেই বলেছি, অর্থনৈতিক বিচারে এমএফএসের ব্যবসা এমএনওর সামগ্রিক ব্যবসার খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ হতে পারে। এমএনওগুলোর এমএফএস খাতে প্রবেশের একটি পদ্ধতি হতে পারে ডাম্পিং কৌশল অবলম্বন, অর্থাত্ এমএনও মালিকানাধীন এমএফএসের জন্য নির্ধারিত মানের বাজারমূল্য থেকে কম দামে কথা বলার সেবা দেয়া, যাতে করে অন্যান্য এমএফএস ব্যবসায় সফলতা হারায় এবং ভবিষ্যতে এ ইন্ডাস্ট্রিতে আর টিকে থাকতে না পারে। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং তা অবশ্যই করতে হবে গ্রাহকস্বার্থ বিবেচনায় রেখে। এছাড়া এমএনওগুলো প্রতিযোগিতাবিরোধী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে পারে। যেমন ৮ মে, ২০১৫-এর ডেইলি স্টারের একটি প্রতিবেদনে টেলিনরের (যা বাংলাদেশের মোবাইল কোম্পানির বৃহত্তর শেয়ারের মালিক) সাবেক প্রধান বলেন যে, ‘তারা হ্যান্ডসেটের মাঝে নির্মিত প্রযুক্তির মাধ্যমে এমএফএস প্রদানের সুযোগ দিতে চায়।’ প্রকৃতপক্ষে যা লকিং পদ্ধতি বা নিজের বাগানে বেড়া দেয়ার মতো এক পদ্ধতি। এ ধরনের আচরণ অন্য এমএনও বা অন্যান্য ব্যাংকের এমএফএসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার পরিপন্থী। এক কথায়, এমএনও তাদের বান্ডেলিং ও লকিং শক্তির দ্বারা মূলধারার এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত করতে পারে।
গ. এমএফএস খাতে বিনিয়োগ অনুত্সাহিত করা: কৌশল হিসেবে এমএনও কিছু সময়ের জন্য এমএফএসকে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছে, যাতে করে এ খাতে অন্যরা বিনিয়োগ করতে অনুত্সাহিত হয়। যেমন— তারা এখন পর্যন্ত একাধিক এমএফএস প্রতিষ্ঠানকে ন্যায্যমূল্যে নেটওয়ার্কের সংযোগ দেয়নি, যা এ ইন্ডাস্ট্রির সঠিক প্রতিযোগিতার বিষয়টি নষ্ট করে। ফলে এমএফএসের আগ্রহী অনেক ব্যাংক বড় ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ করাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। আগের আলোচনার ধারাবাহিকতায় আবারো উল্লেখ্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এমএনওগুলো এমএফএসে মালিকানার সুযোগ দেখছে, ততক্ষণ এ-জাতীয় অসম অবস্থান জিইয়ে রাখবে। এমএফএস খাতে এমএনওর সুযোগ বন্ধ করেও সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করে সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি, অংশগ্রহণ ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানো সম্ভব। উল্লেখ্য, এ ব্যবসায় মূল খরচের খাত হচ্ছে দুটি; প্রথমত. মাঠপর্যায়ে এজেন্টদের প্রস্তুত করা, দ্বিতীয়ত. সাধারণ মানুষকে এমএফএসের সুবিধা ও ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ দুটি কাজই সফলতার সঙ্গে বিগত চার বছরে করা গেছে। কাজেই ব্যাংকগুলোর জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঝুঁকি দুই-ই সমানভাবে কমে এসেছে।
গ্রাহকদের স্বার্থ তুলে ধরার চ্যালেঞ্জ:
ক. আন্তঃক্রিয়াশীলতার সমস্যা: এমএফএসের একজন গ্রাহক অন্য একজন গ্রাহক বা ব্যবহারকারীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করতে চাইবে এবং করতে সক্ষম হবে, এমনটাই স্বাভাবিক। এ কাজ ব্যাহত হবে যদি একটি নির্দিষ্ট এমএফএস একটি এমএনওর মালিকানাধীন হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে অন্য এমএনও এই এমএফএসের সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না-ও চাইতে পারে। এক্ষেত্রে যদি কিছু এমএনও নির্দিষ্ট এমএফএসের হয়ে পক্ষপাতিত্ব, সন্দেহ কিংবা দ্বন্দ্ব-বিরোধ বা সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিঃসন্দেহে আন্তঃক্রিয়াশীলতার সম্ভাবনাকে নস্যাত্ করবে। পক্ষান্তরে যা এমএফএস ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন এবং গ্রাহক অধিকার ব্যাহত করবে। সে কারণে নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার ও সার্ভিস প্রোভাইডার একই মালিকানাধীন হওয়া বাজার ও গ্রাহকস্বার্থের পরিপন্থী।
খ. বাজার চাহিদার বিপরীত: এমএনও সাধারণ জনগণকে দৈনন্দিন জীবনে মোবাইলের মাধ্যমে নানা ধরনের সেবা প্রদান করে। গ্রাহকদের কেউ কথা বলে, কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। অন্যদিকে এমএফএসের গ্রাহকরা অর্থনৈতিক লেনদেন করে। একদিকে এমএনও ও এমএফএসের যেমন গ্রাহকভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন বাজার আছে, অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন সেবা ও ব্যবসায়িক খাতে তারা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। যদি এমএনওগুলো এয়ারটাইম, তথ্যসেবা প্রদান এবং তাদের মালিকানাধীন এমএফএসের সেবা একসঙ্গে বান্ডেল করে গ্রাহকদের আকর্ষণ করে, তা প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির সঙ্গে কখনই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।
গ. দুর্বল ট্র্যাক রেকর্ড: এমএনওগুলো বৃহত্ ক্ষমতাধর কোম্পানি হলেও বাস্তবে ব্যাংকিং সেবাবহির্ভূত দরিদ্র মানুষের ব্যাংকিং সেবা দেয়ার জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি তাদের নেই। এছাড়া বাস্তবে এমএনওগুলোর মালিকানাধীন এমএফএস কার্যক্রমে একে অন্যের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়াশীলতার নজির নেই। উদাহরণস্বরূপ কেনিয়া ও পাকিস্তানের কথা আসে, যেখানে এমএনওগুলো এমএফএস সেবা দিচ্ছে। কিন্তু সেখানেও আন্তঃক্রিয়াশীলতা দীর্ঘদিন সেবা দেয়ার পরও অনুপস্থিত; গ্রাহকরা লেনদেন করতে পারে কেবল নিজেদের নেটওয়ার্কে সীমাবদ্ধ গ্রাহকদের সঙ্গে। তাছাড়া এমএফএস তাদের জন্য খুবই ছোট এবং প্রান্তিক ব্যবসা। তাদের মূল এমএনও ব্যবসার ব্যাপ্তি ও মুনাফা তাদের ক্ষুদ্র মুনাফার এমএফএস ব্যবসার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী করে না। এমএনওগুলো এমএফএসের সেবা দেয়ার মাধ্যম হিসেবে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং এর গভীরতায় প্রবেশে ভালো কাজ করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ টেলিনরের পাকিস্তানে একটি এমএফএসের কার্যক্রম আছে। তাদের এ কার্যক্রমের বয়স বাংলাদেশ থেকে দুই বছরের পুরনো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সত্যিকারের লেনদেনের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রদর্শিত টেলিনরের কর্মক্ষমতা বাংলাদেশের এমএফএসের এক-চতুর্থাংশের কম।
এমএনওর নিষ্ক্রিয়তা ও বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জ
ক. অনাগ্রহী: আগের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখেছি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১১ সালে এমএনওর এমএফএস মডেল খারিজ করেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৫ সালের জুলাই থেকে নতুনভাবে কাজ শুরু করেছে, যেখানে এমএনওকে নতুন করে ছোট আকারের সুযোগ দেয়ার কথা ভাবা হয়েছে। যদিও এমএনওগুলো এমএফএসকে ছোট আকারের শেয়ারের জন্য বিনিয়োগ করতে উত্সাহিত নয়। প্রাথমিকভাবে এমএনওর প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হয়নি। টেলিনরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা টোরে জনসন ২০১৫ সালের ৩ অক্টোবর ডেইলি স্টারে প্রতিবেদনে বলেন, ‘কনসোর্টিয়ামটি ব্যাংক নাকি মোবাইল অপারেটরের নেতৃত্বে চলবে, এ সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হবে। বিভক্ত মালিকানা ভালো পথ নয়।’ একই সংগঠনের আরেক কর্মকর্তা কয়েক মাস আগে ৩০ জুলাই ২০১৫ সালে ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে বলেন, উচিত হবে তাদের (টেলিনরকে) ব্যাংক কিনতে দেয়া।
খ. বাড়তি জটিলতা: এমএফএসে এমএনওগুলোর ছোট আকারের শেয়ারের বিনিয়োগ নতুন ধরনের জটিলতা বাড়াতে পারে। প্রস্তাবিত গাইডলাইনে এমএনওগুলোর জটিল গঠনপ্রণালি দেয়ার কারণে আন্তঃশেয়ারহোল্ডারদের ইস্যু জটিল হয়ে গেছে। এমএনওর শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানা কম থাকার কথা বলা হলেও অন্য শেয়ারহোল্ডারদের তুলনায় করপোরেট পেশিবলে এমএনও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। এমএনওগুলো সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার হওয়া সত্ত্বেও নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসের সম্পৃক্ততার কারণে অন্য শেয়ারহোল্ডারদের তুলনায় বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে, যা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে।
তাছাড়া শেয়ারহোল্ডার নয়, এমন কোনো একটি এমএনও যদি সমস্যা সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে এমএফএস সেবাদানকারী কোনো ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি তাদের নিয়ন্ত্রকের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে। অন্যদিকে যদি কোনো একটি শেয়ারহোল্ডার এমএনও একই সমস্যা সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের কাছে বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার আগেই নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে (উদাহরণস্বরূপ মালিকানা ও কর্তৃত্ব পৃথক করে) এর সমাধানের চেষ্টা করবে। এ ধরনের অসম অবস্থান ইন্ডাস্ট্রির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে, যা এ খাতের প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা কমিয়ে দিতে পারে।
মোবাইলভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নের ভবিষ্যত্ চ্যালেঞ্জগুলো:
ক. মৌলিক ধরনের অবস্থান পরিবর্তন: যদি এমএনওগুলোর এমএফএস করার অনুমোদন দেয়া হয়, তাহলে এটি এমএনওগুলোর ব্যবসার ধরনের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনবে। সাধারণভাবে বলা যায়, এমএনওগুলোর কাজ হলো, কথোপকথনের জন্য সংযোগ সুবিধা তৈরি করে দেয়া; গ্রাহকরা যার মাধ্যমে কথাবার্তা বলে সেবা নিয়ে থাকে এবং তারা সেবা গ্রহণের জন্য এমএনওকে অর্থ দেয়। একইভাবে এমএফএস প্রদানকারীরা এমএনওর বড় ক্রেতা অর্থাত্ এমএফএসদের আর্থিক সেবা প্রদান করা হয় এমএনওর নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে। আর এমএফএস প্রদানকারী সংস্থাগুলো গ্রাহকদের আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। অন্যভাবে বললে, এমএফএসের গ্রাহকই এমএনওর বৃহত্তর সংযোগ ব্যবহারকারী, যারা এমএফএসের নেটওয়ার্ক সেবা গ্রহণের মূল্য হিসেবে এমএনওকে বড় অঙ্কের অর্থ দেয়। যদি এমএনওগুলো নিজেরাই এমএফএস কার্যক্রম আরম্ভ করে, সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব ম্যান্ডেট থেকে সরে দাঁড়াবে। এমএনওগুলো তাদের নেটওয়ার্ক বা সংযোগের বাইরে গিয়ে এবং নিজেদের অন্য নানা ব্যবসায়িক আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যত্ মোবাইলভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিতে এ ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আনার আগে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকির বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা উচিত।
খ. নতুন শিল্পের জন্য হবে ঝুঁকিপূর্ণ উদাহরণ: এমএফএসের মতো নতুন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম যেমন (তথ্যের বিতরণ, বিনোদন, মেডিকেল ডায়াগনস্টিক, কৃষি, বাজার) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (এমএনওর সংযোগ ব্যবহার করে) করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা উত্তরোত্তর বাড়বে। ফলে এমএনওগুলো এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে বড় অঙ্কের আয় বাড়াতে পারবে। যদি এমএনওগুলোর নেটওয়ার্ক বা সংযোগের বাইরে এমএফএস মালিকানায় অংশ নেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে বিমাতাসূলভ আচরণ করা হবে। এমএনওগুলোর কার্যক্রম নেটওয়ার্ক বা সংযোগের মধ্যে যথাযথভাবে সীমিত রাখা না গেলে নতুন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমগুলো ভবিষ্যতে কখনই সফলকাম হতে পারবে না। কারণ নেটওয়ার্ক বা সংযোগের মালিকানার জন্য যেকোনো নতুন শিল্পের উত্থান পর্বে এমএনওগুলো অগ্রবর্তী কিংবা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাবে।
উপসংহার: উপরের পর্যবেক্ষণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্ধারকদের কী করা উচিত? বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এর সমাধান বিশেষভাবে নির্ভর করবে এমএফএসের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের ওপর। এমএফএসের কার্যকর পরিচালনার ওপরই এ খাতের আরো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করছে। অর্থাত্ বিষয়টি এমন দাঁড়াচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমএফএসকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ সিলিং নির্ধারণ করবে। এমএফএস তাদের দক্ষতা ও পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থিক সেবার উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবে।
সুস্পষ্টভাবে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমএনওগুলোর ব্যাপারে। আর উত্সাহিত করতে হবে, যাতে সরকারি ও অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংক, বিশেষত দেশী বিনিয়োগকারী এমএফএসে বিনিয়োগ করে। এমএনওগুলোর বাইরে রেখে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা, যেখানে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতাময় সমতল ক্ষেত্র তৈরি হয় আর পাশাপাশি এমএফএসের নতুন বিনিয়োগকারী উত্সাহিত হয়। এমএফএসে নতুন প্রবেশকারীরা যেন সাবলীলভাবে কাজ করতে পারে। দুটি কারণে এমএফএসে নতুন বিনিয়োগ বাড়বে। প্রথমত. বাজার এরই মধ্যে বিষয়টি প্রমাণ করেছে এবং ক্রেতারা এমএফএসের সুযোগ-সুবিধা ও কাজ সম্পর্কে অবগত। এসব কারণে ব্যাংক ও অন্য নিয়োগকারীরা এমএফএসে বিনিয়োগে আকর্ষিত হবে। ফলে বাজারে অনেক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হবে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রস্তাবিত গাইডলাইনের ভিত্তিতে যথাযথ সাহসী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়। দ্বিতীয়ত. নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান প্রয়োজন, নতুন কাজের জন্য নতুন যে দক্ষতা এবং ক্রেতাদের সচেতনতা দরকার, বাংলাদেশে এরই মধ্যে তা তৈরি হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এবং এরই মধ্যে খাতটির অর্জিত সাফল্যকে দেশের মধ্যে ধরে রাখা ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এমএফএসের স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করতে সহায়তা দিতে হবে। এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও সহায়তার মাঝেই খাতটির ভবিষ্যত্ সম্ভাবনা নিহিত।
লেখক: সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি
সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ইউএসএসডি টেকনিক্যাল কমিটি (২০১৪)
Source







